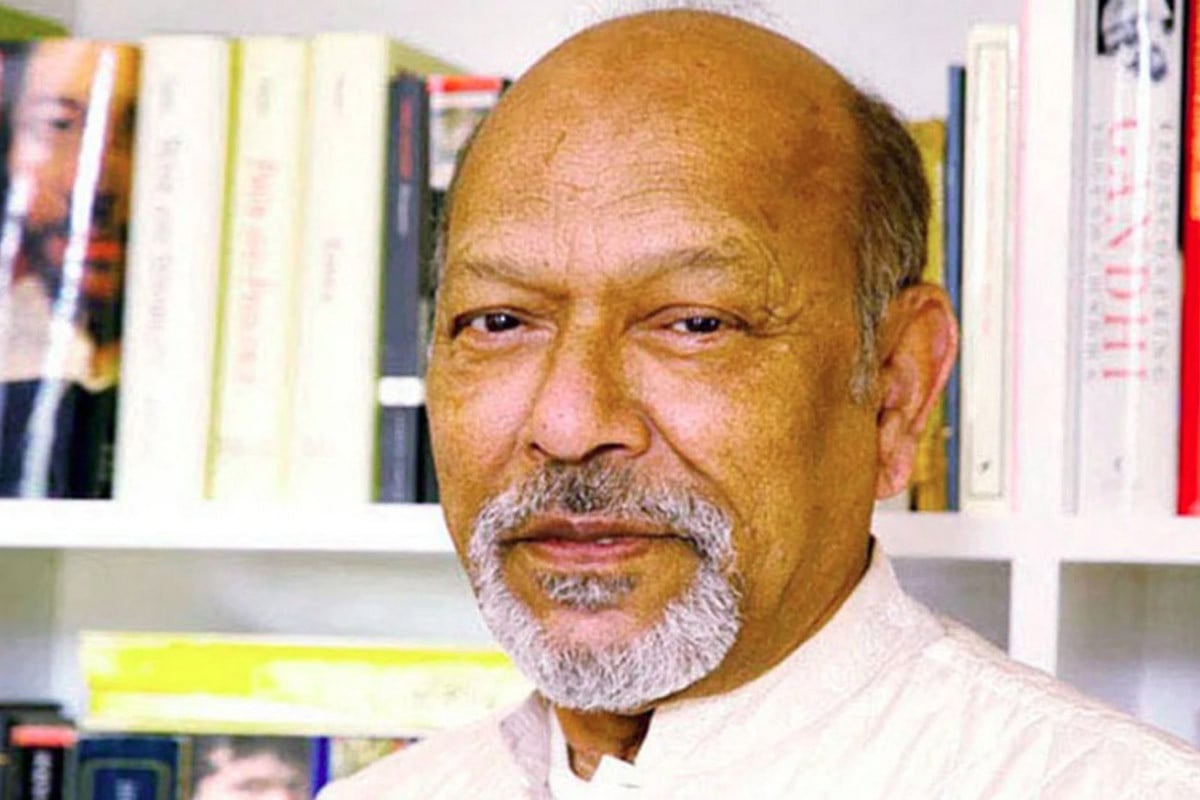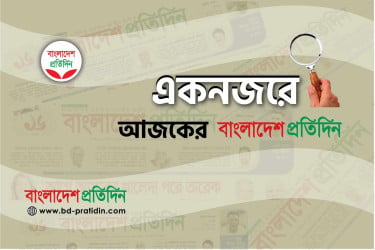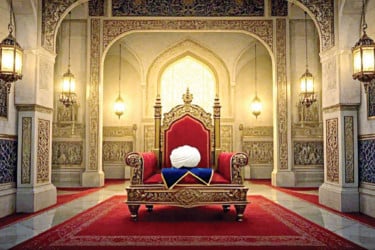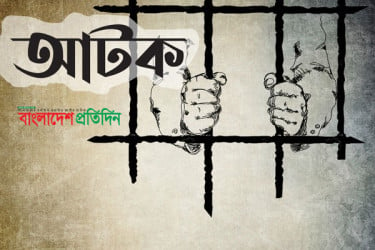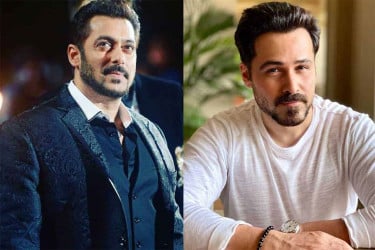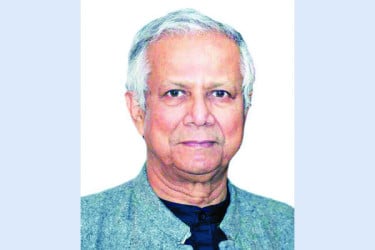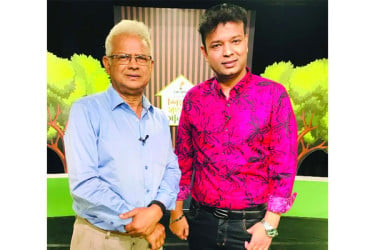এক. আসন্ন ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম নগর নির্বাচনে প্রার্থীরা নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য নানা প্রকার অঙ্গীকার করছেন। তার মধ্যে 'নগর সরকার' বাস্তবায়নের বিষয়টিও রয়েছে। শুধু প্রার্থীরাই নন, বেশকিছু বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও এনজিও ব্যক্তিত্বও 'নগর সরকার' বাস্তবায়নের কথা বলছেন। এটি নিঃসন্দেহে রাজনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের পেছনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিডিএলজির সামান্য হলেও অবদান রয়েছে। এটি বিলম্বে হলেও অনেকেই এখন স্বীকার করছেন। যেমন- সম্প্রতি দৈনিক সমকালে প্রকাশিত 'কবে হবে নগর সরকার' শীর্ষক একটি রিপোর্টে বলা হয়- 'ঢাকার জন্য প্রথম নগর সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে ১৯৯৭ সালে। ওই বছরের ১৩ জানুয়ারি সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক লোকাল গভর্ন্যান্স (সিডিএলজি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকায় জাতীয় সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধে নগরবাসীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নত দেশগুলোর মতো ঢাকার জন্য একটি নগর সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমে একটি সিটি পার্লামেন্ট নির্বাচন করা হবে। সিটি পার্লামেন্টের নির্বাচিত কাউন্সিলরদের ভোটে একজন মেয়র নির্বাচিত হবেন, যিনি হবেন নগর সরকারের প্রধান।' রিপোর্টটিতে একটু ভুল আছে, তা হলো- 'সিডিএলজি' নয়, ওই সেমিনারে নগর সরকারের কথা প্রথমে বলেন স্থানীয় সরকারবিষয়ক গবেষক নিউইয়র্ক প্রবাসী আবু তালেব। পরবর্তীকালে তারই পরামর্শে 'সিডিএলজি' গঠন করা হয়। তা ছাড়া সংগঠনটির নগর সরকারের রূপরেখায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে মেয়র নির্বাচনের কথা বলা ছিল না। মেয়র নগরবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন, এমনটিই ধারণা দেওয়া হয়েছিল। তবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে নগর সরকার পরিচালনার বিষয়টি অধিকতর পর্যালোচনার দাবি রাখে।
দুই. ২০২০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ নগরায়ণসহ অন্যান্য পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে স্বাবলম্বী, সশাসিত ও গতিশীল স্থানীয় সরকার স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে উল্লিখিত সেমিনারে 'গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের রূপরেখা' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। সেদিন নগর সরকারের রূপরেখাও তুলে ধরা হয়। এর কিছুদিন পর ঢাকার তৎকালীন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ মেট্রোপলিটান গভর্নমেন্টের প্রস্তাব করেন। তখন আবু তালেব মেয়র হানিফের কাছে গিয়ে বলেন, 'ঢাকার লোকসংখ্যা যখন কোটি ছাড়িয়ে যাবে তখন কী মেগাসিটি গভর্নমেন্ট বলা হবে! তার চেয়ে সমগ্র দেশের জন্য একরূপ নগর সরকারের কথা বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।'
সেদিনকার বৈঠকে চট্টগ্রামের এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ইংরেজিতে সিটি গভর্নমেন্টের কথা বলা শুরু করেন। কিন্তু সিটি গভর্নমেন্ট বলতে কী বুঝায়, এর রূপরেখা কেমন এবং এটি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। যা হোক, পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের রূপরেখাটি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে সিডিএলজি গঠন করা হয়। তারপর থেকে সিডিএলজি বিষয়টি নিয়ে লাগাতার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত রূপরেখাটির সারসংক্ষেপ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, রাজনীতিক, গবেষক, লেখক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, এনজিও ব্যক্তিত্বসহ সংশ্লিষ্ট সবার অবগতি ও বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। এর পাশাপাশি বৈঠক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার, মতবিনিময় সভা, দলগত সভা, একজন একজন করে মতবিনিময় সভা, টেলিসংলাপ, প্রকাশনা, পত্রিকায় লেখালেখি, ই-মেইলে গবেষণা প্রেরণ ইত্যাদিও চালু রয়েছে।
তিন. আরও উল্লেখ্য, সংবিধানের বাংলা ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি মাত্র সরকারব্যবস্থা রয়েছে। সেটিও অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। বিদ্যমান স্থানীয় সরকারগুলো ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল, উন্নয়নের প্রয়োজনে নয়। তারপরও ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় সরকারগুলোকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছিল বর্তমানে সেটুকুও নেই। যেমন- জেলা বোর্ডগুলোর হাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয়গুলো ন্যস্ত ছিল। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল এক জেলা থেকে আরেক জেলামুখী তথা আনুভূমিক। ঢাকামুখী ব্যবস্থাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাকিস্তান আমলে সর্বপ্রথম ঢাকামুখী আনুলম্বিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে বড় বড় সড়ক ও সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে রাজধানী ঢাকাকে সামনে করে। সব কিছু ঢাকামুখী হওয়ায় ঢাকার লোকসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকাকে বাঁচাতে এখন অনেকেই সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ চাচ্ছেন। কেউ কেউ তিন ধরনের সরকারব্যবস্থার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদির বাস্তবায়ন চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সিডিএলজির বক্তব্য হলো- এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আয়তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় নিলে মূলত দুই ধরনের সরকারব্যবস্থা তথা একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও একটি সমন্বিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থাই বাস্তবায়নযোগ্য। কেন্দ্রের হাতে শুধু জাতীয় ও বৈশ্বিক কাজগুলো নির্দিষ্ট থাকবে। আর অবশিষ্ট সব স্থানীয় কাজ জেলাকেন্দ্রিক থাকবে। জেলার চরিত্র হবে গ্রামীণ-নগরীয়। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার হবে দুই-স্তরবিশিষ্ট। জেলা এক হাতে নগর সরকারগুলো অর্থাৎ পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনগুলো এবং আরেক হাতে উপজেলা সরকার (ভবিষ্যতে যদি এটির প্রয়োজনীয়তা থাকে) ও ইউনিয়ন সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ব্যবস্থায় সমগ্র দেশে ৩৩০টি (১১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি করপোরেশন) একরূপ 'নগর সরকার' হবে। সংক্ষেপে নগর সরকারের রূপরেখা তুলে ধরা যেতে পারে : নগর সংসদ, নগর প্রশাসন, নগর আদালত মিলে 'নগর সরকার' গঠিত হবে। কাউন্সিলররা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। তারা নগর সংসদের সদস্য হবেন। বর্তমানে 'কাউন্সিল' নেই, কিন্তু কাউন্সিলর আছেন। নগর সংসদ সদস্যরা মিলিতভাবে একজন সভাপতি (স্পিকার) নির্বাচিত করবেন। মেয়রও নগরবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। তিনি নগর সংসদের সদস্য হবেন না। তিনি নগর সংসদের পাসকৃত প্রস্তাবাবলি তার প্রশাসন দ্বারা বাস্তবায়ন করবেন। মেয়র হবেন নগর প্রশাসনের প্রধান। তার অধীনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিয়োজিত থেকে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করবেন। তা ছাড়া মেয়র ফুলটাইমার এবং কাউন্সিলররা পার্টটাইমার হিসেবে দায়িত্বরত থাকবেন। নগর সংসদ ও নগর প্রশাসনের বাইরে 'নগর আদালত' থাকবে। মেয়র ও কাউন্সিলররা নগর আদালতের সদস্য হবেন না। বর্তমানে কাউন্সিলররা বিচারিক দায়িত্বও পালন করছেন। আলাদাভাবে নির্বাচিত কিংবা নিয়োজিত ব্যক্তিরা নগর আদালতের বিচারক হবেন। তারা নগরকেন্দ্রিক নির্দিষ্ট অপরাধ ও অন্য বিরোধগুলোর বিচার করবেন। নগর সরকারের বাইরে একজন নগর ন্যায়পাল (শেরিফ) থাকবেন। তিনি নগর সংসদ ও নগর প্রশাসনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করবেন। এর বাইরে একটি নগর নির্বাচনিক বোর্ড থাকবে। নগরের গণ্যমান্য কিংবা মনোনীত ব্যক্তিরা নগর নির্বাচনিক বোর্ডের সদস্য হবেন। তারা নগর সরকারের মেয়াদ শেষে নিজেদের উদ্যোগে নির্বাচনের আয়োজন করবেন, যা অনেকটা প্রেসক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনের মতো। এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সত্যিকার সশাসিত নগরব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তখন নগর হবে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তখন প্রত্যেক নাগরিক নগর সরকারের অংশ হয়ে যাবেন।
চার. ইদানীং কয়েকজন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ পার্লামেন্টারি পদ্ধতির স্থানীয় সরকার হলে জনগণের পক্ষে সরকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি হবে। বিষয়টি অযৌক্তিক নয়। তবে তারা আবার স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অরাজনৈতিকভাবে হওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির স্থানীয় সরকার হলে তো রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি তৃণমূলের দলীয় কর্মীরা আরও জোরালোভাবে দাবি করবে, এতে কী কোনো সন্দেহ আছে?
পাঁচ. অব্যাহত নগরায়ণ ও নাগরিক সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের কোনো বিকল্প নেই। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের কোথাও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন স্থানীয় সরকারের একমাত্র রূপ হবে নগর সরকার। তাই আমরা সিডিএলজির পক্ষ থেকে বলতে চাই, নগর সরকার আমাদের বর্তমান ও আগামীর বাংলাদেশের জন্য এক নিদারুণ বাস্তবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি আমরা এটি বুঝতে সক্ষম হব, আমরা তত দ্রুত সার্বিক অগ্রগতির দিকে সফলভাবে এগিয়ে যাব, এটি নিশ্চিত বলা যায়।
লেখক : চেয়ারম্যান, জানিপপ, সহলেখক : ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান, ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার, জানিপপ এবং মোশাররফ হোসেন মুসা, সদস্য, সিডিএলজি ও ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার, জানিপপ।
ই-মেইল- [email protected]