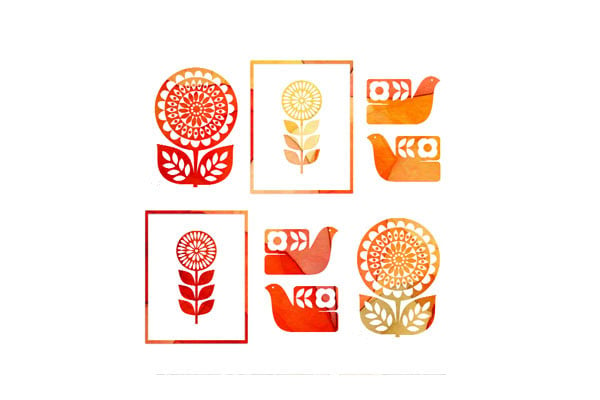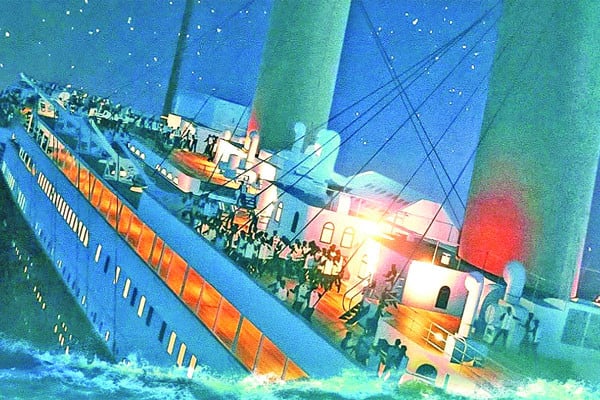আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের কথা বলি। গণতন্ত্রের একেবারে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, কিন্তু সেটা যে অর্জন করতে পেরেছি তা বলতে পারব না। সাম্প্রদায়িকতা কমেছে, কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বরঞ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে, কমবার লক্ষণ নেই। পয়লা বৈশাখ সর্বপ্রথম যে-কথাটা বলে, সে-কথা ধর্মনিরপেক্ষতার। ব্যক্তির জীবনে ধর্ম আছে, থাকুক, কিন্তু সমষ্টিগত পরিচয়টা ধর্মের ভিত্তিতে হবে না, হবে মাতৃভাষার ভিত্তিতে। কথা তো এটাই।
যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যুদ্ধ করলাম সে-রাষ্ট্র যে ধর্মনিরপেক্ষ হবে এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। হানাদার পাকিস্তানিরা ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা একটি ধর্মযুদ্ধে নেমেছে; আমরা বলেছি, তারা নিয়োজিত হয়েছিল বাঙালি নিধনে। আমাদের ওই বক্তব্য কোনো তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙালির ওই প্রতিরোধ শুরু বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। মনীষী বাঙালি লেখকদের যে-বক্তব্য একুশে ফেব্রুয়ারি তাকেই আরও সামনে নিয়ে গেছে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে রাষ্ট্রে ও সমাজে। বড় লেখকরা বাঙালির হৃদয়ে যে সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন সেই সহমর্মিতাকেই আরও প্রসারিত করতে চেয়েছে, শ্রেণির বন্ধন ও বিভেদ ভেঙে দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল ওই আন্দোলনেরই যৌক্তিক পরিণতি।
.jpg)
কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা পেল না কেন? পেল না নেতৃত্বের কারণে। সাধারণ মানুষ ধর্মের কাছে যায় আশ্রয়, ন্যায়বিচার ও ভরসার প্রয়োজনে। রাষ্ট্র ও সমাজে এসবের কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। যে-ব্যবস্থায় লোকে পুলিশকে দেখলে চোর-ডাকাতের চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়, আদালতের ওপর আস্থা যেখানে ন্যূনতম, সেখানে ঈশ্বর ছাড়া কে তাকে বাঁচাবে? কিন্তু তবুও লোকে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে এক করে দেখে না। বৈশাখের সকাল তাকে বলে ক্ষেতে যেতে হবে হাল-চাষের জন্য। অথবা যেতে হবে দিনমজুরির খোঁজে। যত্ন নিতে হবে গরুর, যদি গরু থেকে থাকে। মসজিদের ইমাম সাহেব ভালো লোক, কিন্তু তিনি যে থানার দারোগাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, এই খবর বাংলাদেশের কোন মানুষটি না-জানে, শুনি, উনিশ শ’ ছেচল্লিশে দেশের মানুষ ভোট দিয়েছে জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে মুক্তির আশায়। উনিশ শ’ সত্তরে ভোট দিয়েছে পাকিস্তানি শোষকদের চাপিয়ে দেওয়া জোয়ালটাকে কাঁধ থেকে নামাতে পারবে এই ভরসায়। উভয় ক্ষেত্রেই তার আচরণ বিশুদ্ধরূপে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু নেতৃত্বের আচরণ ভিন্ন রকমের। উনিশ শ’ ছেচল্লিশে নেতৃত্ব ছিল মুসলিম লীগের হাতে। মুসলিম লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নয়, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম করেছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ যে গঠিত হয় সেটা মুসলিম লীগের আদর্শকে পরিত্যাগ করে নয়, ওই আদর্শকে ধারণ করেই। মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র যে ইসলামভিত্তিক হবে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আওয়ামী মুসলিম লীগের কারণে ঘটেনি, ঘটেছে ছাত্রদের কারণেই। আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে আরও পরে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি বিজয়ের পথ ধরে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নেতৃত্ব ছিল পিছিয়ে, জনগণ ছিল এগিয়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নেতাদের অধিকাংশই তো এসেছেন মুসলিম লীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে। ওই রাজনীতির অভ্যাস ও ঐতিহ্য তাঁরা যে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি সেটা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তাঁদের বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা ধর্মকে ব্যক্তিগতকরণের পরিবর্তে বরঞ্চ বুঝেছেন সকল ধর্মের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মের আরও অধিক চর্চা। পঁচাত্তরের পর থেকে তো ধর্মনিরপেক্ষতা সাংবিধানিকভাবেই বাদ পড়ে গেছে। কাজটা বিএনপি করেছে এবং আওয়ামী লীগ মেনে নিয়েছিল। এখন তো বুর্জোয়া সকল দলই ভোটের জন্য ধর্মকে প্রতিযোগিতামূলকভাবেই ব্যবহার করছে। কে কাকে দেখে?
পয়লা বৈশাখ ধর্মকে ঘরে ও প্রার্থনার জায়গাতেই রাখতে চায়, সামাজিক ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে আনতে নিষেধ করে। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে ভক্তিবাদের একটা উপাদান আছে : সে-ভক্তি সাম্প্রদায়িক নয়, কিন্তু তাই বলে যে ধর্মনিরপেক্ষ তা-ও নয়। যিনি আল্লাহ তিনিই হরি-এই ঘোষণা অসাম্প্রদায়িক অবশ্যই, কিন্তু নিশ্চয়ই ধর্মনিরপেক্ষ নয়। কেননা, এতে বিশেষ কোনো ধর্মকে না হলেও, সাধারণভাবে ধর্মকেই জরুরি করে তুলেছে। সংস্কৃতি এই উপাদানটিকে উৎসাহিত করে আমরা যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সাহায্য করতে পারব না, এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন।
মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী একটি আধুনিক পুঁথির ভণিতায় পড়লাম, “আরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লা-নবীর নাম/ রামকৃষ্ণ আর গৌতম বুদ্ধ যীশুরে প্রণাম/ পুরু নাম রাম লক্ষ্মণ আর সরস্বতী/ স্মরণ করি মানবসেবার সকল মহতি/ তারপরেতে স্মরণ করি আল্লাহর কালাম/ মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদের সালাম। ঠিকই আছে কথাগুলো, মনে হবে ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু আসলে তো ধর্ম তো ধর্মনিরপেক্ষ নয়। হ্যাঁ, প্রাচীন পুঁথিতে এরকম শ্রেণিতাই থাকত বটে, কিন্তু আমাদের তো নতুন পুঁথি লিখতে হবে, তাতে প্রাচীন পুঁথির সুর, ছন্দ, শব্দ থাকুক অসুবিধা নেই, কিন্তু তার প্রাণবস্তুটা তো হবে আধুনিক; মুক্তিযুদ্ধের চেতনার-দ্বারা সমৃদ্ধ, এই অর্থে আধুনিক! বলাই বাহুল্য, ওই চেতনার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা।
পয়লা বৈশাখ ধর্মের ভেদাভেদ মানে না, শ্রেণির ভেদাভেদ যে মানে তাও নয়। কিন্তু আবার মানেও তো। বৈশাখের সাতসকালে গরিব মানুষ কোথায়? রমনা বটমূল তো তাদের জন্য বিস্তর দূর, তারা কোনো বটমূলেই নেই, মেলাতেও নয়। তারা ব্যস্ত রয়েছে কাজে, নয়তো কাজের খোঁজে। আমাদের ধর্মীয় পার্বণে গরিব মানুষ আসে, এসে ভিক্ষা চায়, নিজেদের রোগ ও ক্ষতগুলোকে উন্মোচিত করে দেখায়, করুণার উদ্রেক হবে এই ভরসায়। পয়লা বৈশাখে তেমন কোনো অঘটন ঘটে না। তার কারণ একটাই, গরিব মানুষ এই উৎসব থেকে অনেক দূরে থাকে।
মানুষে মানুষে ঐক্য গড়ে উঠেনি, কারণ বৈষম্যের পরিখা গভীর ও প্রশস্ত হচ্ছে একই সঙ্গে। ঠাট্টা করে এক বন্ধু সেদিন বললেন, দেশে ধনীর সংখ্যা ও তাদের ধনস্ফীতি এত বাড়ছে যে, অচিরেই তাদের আয়ের সঙ্গে গরিব মানুষের আয় যোগ করে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে, মাথাপিছু আয়ের হিসাবে আমরা আর অনুন্নত নই। হয়তো তাই। কিন্তু তা দিয়ে তো বোঝা যাবে না যে, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এসে গেছে। ঠিক যেমনভাবে ‘এক মাথা এক ভোট নীতি’ চালু আছে বলেই বলার উপায় নেই যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এক মাথা এক ভোট পাকিস্তানের কবল থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করেছে, কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ হচ্ছে ওই বৈষম্য। সেকালে বৈষম্য ছিল অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের, একালে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির।
মূল কথাটা হচ্ছে বৈষম্য ভাঙা, পয়লা বৈশাখ সেটাকে ভাঙতে বলে, বলে ভাঙতে হবে সম্প্রদায়ের পার্থক্য তো বটেই শ্রেণিগত অসাম্যও। পয়লা বৈশাখ প্রকৃত গণতন্ত্র চায়, ইংরেজি নববর্ষের সঙ্গে এখানে তার মৌলিক তফাত আমাদের প্রিয় ঋতু শীত; বর্ষা মায়ের মতো, শীত যেন বোন। আমাদের সংস্কৃতিতে মায়ের মমতা ও বোনের স্নেহ খুবই দরকার, অন্য সবকিছুর আগে।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়