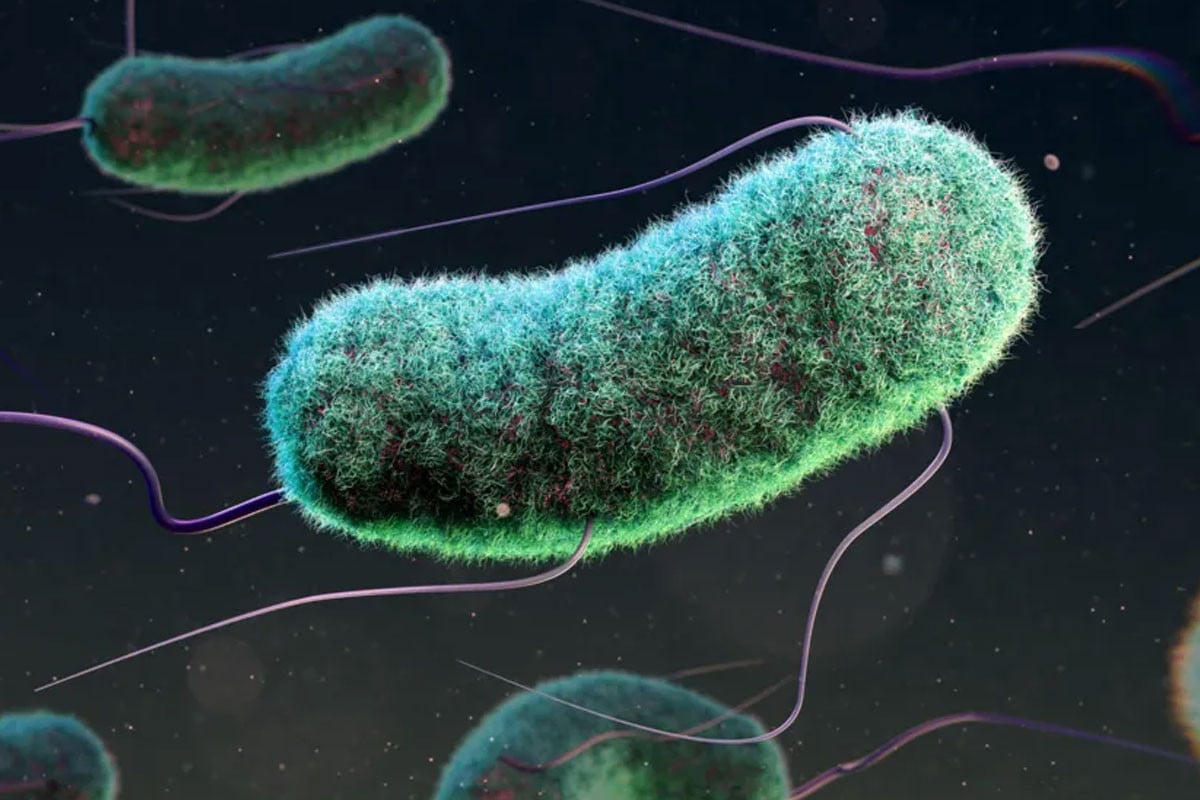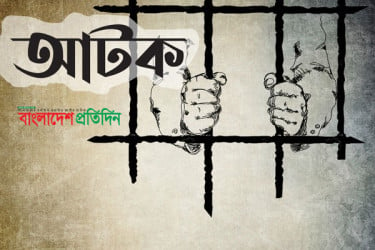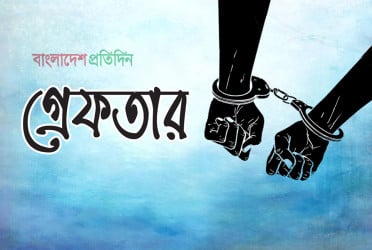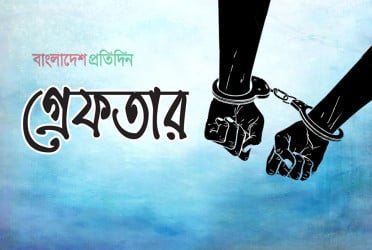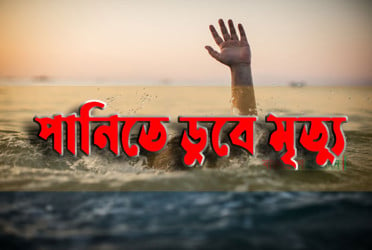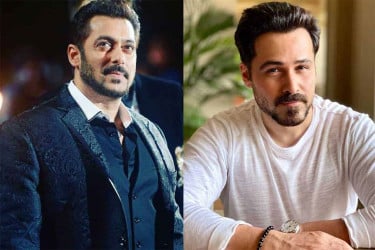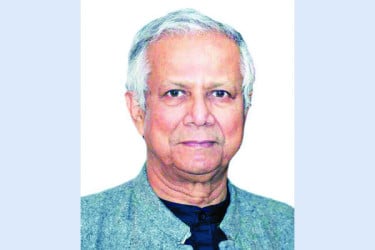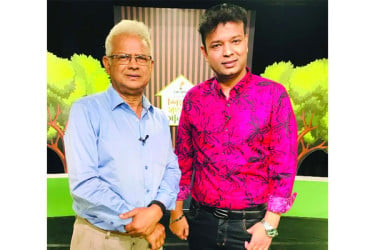পলিসাইথেমিয়া রক্তের একটি বিশেষ অসুখ, যা এনিমিয়ার ঠিক উল্টো। এনিমিয়ায় হিমোগ্লোবিন কমে যায়। পলিসাইথেমিয়ায় যায় বেড়ে। ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি হিমোগ্লোবিন ১৭.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫.৫ গ্রাম/ ডেসিলিটারের বেশি হয়, তাহলে সেটাকে পলিসাইথেমিয়া বলে প্রাথমিকভাবে গণ্য করা হবে।
পলিসাইথেমিয়ার কারণ ও ধরণ
দুরকম কারণে পলিসাইথেমিয়া হতে পারে। অস্থি মজ্জা বা স্টেম সেলের সমস্যাজনিত কারণে পলিসাইথেমিয়া হতে পারে। এটাকে বলে প্রাইমারি পলিসাইথেমিয়া বা পলিসাইথেমিয়া রুব্রা ভেরা।
অপরটি হলো সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়া। যদি শরীরের অন্য কোনো অসুখের প্রতিক্রিয়ায় পলিসাইথেমিয়া দেখা দেয় তবে তাকে বলে সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়া। বিভিন্ন ধরনের টিউমার, কিডনির অসুখ, জন্মগত হার্টের অসুখ, এজমা বা সিওপিডিজনিত ফুসফুসের অসুখ ইত্যাদি কারণে রক্তের উৎপাদক হরমোন ইরাইথ্রোপোয়েটিন বেড়ে যেতে পারে। সেই ইরাইথ্রোপোয়েটিনের প্রভাবে রক্তের লোহিতকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে পলিসাইথেমিয়া হতে পারে।
আরেকধরনের পলিসাইথেমিয়া আছে। সেটা হলো রিলেটিভ পলিসাইথেমিয়া। অর্থাৎ আসলে কোষের সংখ্যা বাড়েনি কিন্তু রক্তরসের অনুপাতে রক্তকোষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অতিরক্তি ধূমপান, মদ্যপান, মূত্রবর্ধক ওষুধ ইত্যাদি কারণে রক্তরস কমে গিয়ে রক্তকোষের আনুপাতিক বৃদ্ধি হতে পারে।
পলিসাইথেমিয়া হলে কী হয়?
পলিসাইথেমিয়ায় রক্তকোষ বেড়ে গিয়ে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। ফলে মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট, চোখে কম দেখা, চুলকানি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। গরম পানিতে গোসল করলে গা বেশি করে চুলকায়।
পলিসাইথেমিয়ায় রোগীর চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। তাই এর নাম রুব্রা ভেরা। অবশ্য এশীয় মহাদেশীয় বাদামি ত্বকের রোগীর ক্ষেত্রে লাল হয়ে যাওয়ার বদলে বলতে হবে কালো হয়ে যায়। এ ছাড়া প্লীহা বড় হয়ে যায়, ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, পেপটিক আলসার, জয়েন্টে ব্যথা ইত্যাদিও দেখা দিয়ে থাকে।
রক্তের ঘনত্ব বাড়তে থাকলে বিপদও বাড়তে থাকে। রক্ত ঘন হয়ে আস্তে আস্তে রক্তের প্রবাহ ধীর হয়ে যায়। স্ট্রোক, হার্টঅ্যাটাক ইত্যাদির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
রোগ নির্ণয়ে কী কী পরীক্ষা করা হয়?
রক্তের ফিল্ম (সিবিসি) পরীক্ষাতেই প্রাথমিকভাবে রোগটি ধরা পড়ে। হিমোগ্লোবিন ও পিসিভি বা হিমাটোক্রিটের মাত্রা দেখে রোগটির প্রাথমিক নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এরপরের ধাপে দেখতে হয়ে সেকেন্ডারি কোনো কারণে এটি হয়েছে কি না। রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস সেক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাথে টিউমার মার্কার পরীক্ষা, বুকের এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, হার্টের ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইসিজি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ইরাইথ্রোপোয়েটিনের মাত্রা পরীক্ষা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আমাদের দেশে এর সুযোগ খুব কম। প্রাইমারি কারণ বা মজ্জার সমস্যাজনিত কারণে হয়েছে বলে মনে হলে বোনম্যারো পরীক্ষা ও বিশেষ জিনের মিউটেশন দেখার জন্য সাইটোজেনেটিক পরীক্ষা করা হয়।
চিকিৎসা কী?
এই রোগের চিকিৎসা তুলনামূলক সহজ। এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা ভেনিসেকশন। ভেনিসেকশন মানে হলো শিরায় সুঁই ফুটিয়ে রক্ত টেনে নিয়ে ফেলে দেওয়া। যেভাবে ব্লাড ডোনারদের থেকে রক্ত নেওয়া হয় সেভাবেই। তবে এই রক্ত কাউকে দান করা যাবে না। রোগের মাত্রাভেদে চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সপ্তাহে একবার বা একাধিকবার ভেনিসেকশন করা যেতে পারে।
ওষুধের মধ্যে আছে হাইড্রোক্সিইউরিয়া, বুসালফেন। মিউটেসন স্টাডি করে পজিটিভ পাওয়া গেলে জ্যাকাফি নামক এক প্রকার ওষুধ দেওয়া যায়। তবে আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুবই সীমিত। কারণ, এর দাম সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে।
একটু বেশি বয়সী যারা, তাদের ক্ষেত্রে রেডিও এক্টিভ ফসফরাস ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন কারণে এটিরও ব্যবহার সীমিত।
রোগের পরিণতি
প্রাইমারি পলিসাইথেমিয়ার রোগী নিয়মমাফিক চিকিৎসা নিলে ও নিয়মিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধায়নে থাকলে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে। পাঁচ শতাংশ রোগী পরবর্তীতে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। ২০-৩০ শতাংশ রোগী মাইলোফাইয়াব্রোসিস নামক এক প্রকার মজ্জার জটিল অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়ার ক্ষেত্রে মূল যে রোগ সেটির চিকিৎসা করলে পলিসাইথেমিয়াও ভালো হয়ে যায়।
লেখক: রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
বিডি প্রতিদিন/জুনাইদ আহমেদ