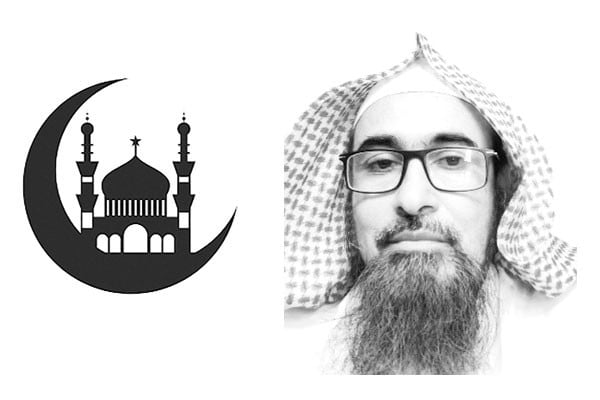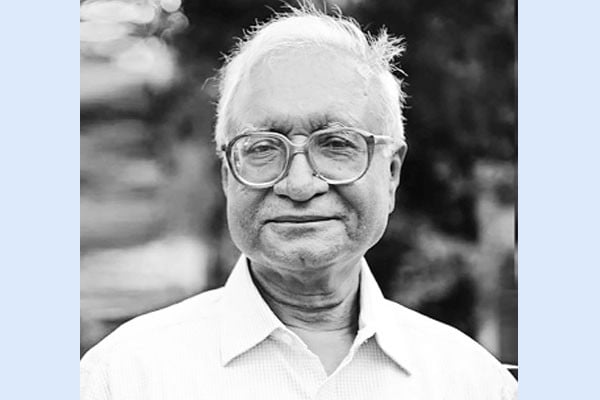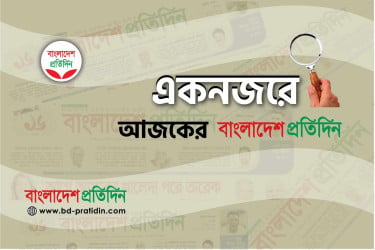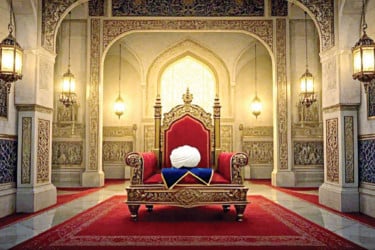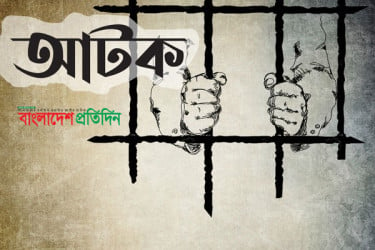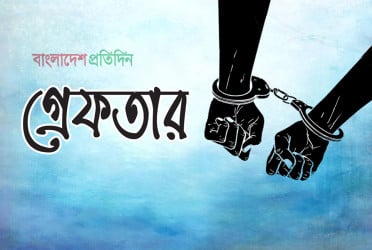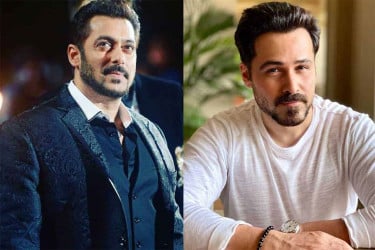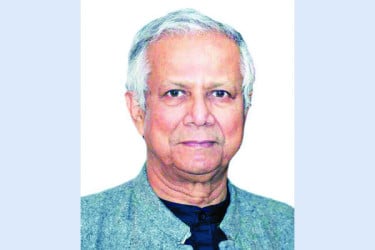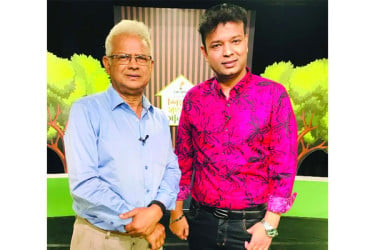জাতিসংঘের জলবায়ু রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তীব্র খরা, জলোচ্ছ্বাস ও ভয়াবহ বন্যার দিকে। উষ্ণায়নের এই নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে অনেক আগে থেকেই ভাবতে বসেছে উন্নত দেশগুলো। তাই তারা নগরকে বহু বছর ধরে সাজাচ্ছে তাদের মতো করে। এমনকি কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যেও আনছে নতুন নতুন পরিবর্তন।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার বিবেচনায় ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৬৭ ভাগ লোক চলে আসবে নগর এলাকায়। একদিকে নগর ধেয়ে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের দিকে। গ্রামীণ জীবন ও সমাজ নগরায়ণের প্রভাবে পাল্টে যাচ্ছে। অন্যদিকে অব্যাহত রয়েছে নগরমুখী মানুষের স্রোত। আমাদের ঢাকা শহরের বাস্তবতাই জানান দেয় সে কথা। প্রশ্ন হলো, নগর যদি মানুষের এই চাপ সামাল দিতেও পারে, তাহলে খাদ্য জোগান নিশ্চিত হবে কীভাবে? পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো এ ভাবনায় যথেষ্টই অগ্রসর। তার মানে নগরের মানুষও কৃষি থেকে পিছিয়ে নেই। আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে, নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে ‘ছাদে বাগান’ গড়ার একটি অভিযান শুরু করেছিলাম। আবার হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে নগরকৃষির উদ্বুদ্ধকরণ অভিযান শুরু করেছি বেশ আগে। বিশেষ করে নগরের মানুষকে কৃষিতে অনুরক্ত করে তোলা ও প্রজন্মের কাছে কৃষির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা থেকেই এসব উদ্যোগ। আমরা কখনোই গ্রামের মানুষের বিশেষ করে কৃষকের সমস্যাটি তেমনভাবে অনুধাবন করতে পারি না। এর প্রধান কারণ নীতিনির্ধারকরা মূলত সবাই শহরে বসবাস করেন। আর একটা বিষয় আমরা আমলে নিচ্ছি না। সেটা হলো, গ্রামগুলো ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হবে। আগামীর কৃষি হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কৃষি। এক অর্থে নগরকৃষি।
আমার বড় ছেলে অয়ন একজন স্থপতি। একদিন জানাল চীনের সাংহাইয়ে সানকিয়াও আরবান ফার্মিং ডিস্ট্রিক্ট নামের একটা প্রজেক্টের কথা। যেখানে ১০০ হেক্টর জমির ওপর তৈরি হচ্ছে আধুনিক কৃষিনগরী। কৃষি তো এখন শুধু মাঠের বিষয় নয়। কৃষির সম্প্রসারণ হবে ঊর্ধ্বমুখী। বিশ-বাইশতলা বিল্ডিংয়ের ভিতর নিয়ন্ত্রিত আলো-বাতাসে চাষ হবে সতেজ ফসলের। যেমন নেদারল্যান্ডসে টেলিকমিউনিকেশনস প্রতিষ্ঠান ফিলিপসের বাতিল করে দেওয়া ছয়তলাবিশিষ্ট বিশাল ভবনটি হয়ে উঠেছে ইউরোপের সবচেয়ে বড় নগরকৃষির ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাগুলোর বরাতে আরও তথ্য দেওয়া যায়। জাপানে নগরে বসবাসরত ২৫ ভাগ পরিবার কৃষির সঙ্গে যুক্ত। টোকিও শহরে প্রায় সাত লাখ নাগরিকের সবজি আসে নগরকৃষি থেকে। নিউইয়র্কে প্রায় ১০০ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে নগরকৃষিতে। কেনিয়ার নাইরোবিতে খাদ্যপ্রতুলতার জন্য চলছে নগরকৃষি কার্যক্রম। আর জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে ৮০ কোটি লোক নগরকৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। যারা মোট উৎপাদিত খাদ্যের ১৫-২০ ভাগ উৎপাদন করে। নেদারল্যান্ডস নগরকৃষিতে সমৃদ্ধ বলেই ছোট্ট দেশ হয়েও নিজেদের চাহিদা পূরণ করে সারা পৃথিবীতে সম্প্রসারণ করতে পেরেছে খাদ্যপণ্যের বাণিজ্য। হংকংয়ে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নগরকৃষির সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়াও হংকংয়ে ‘রুফটপ রিপাবলিক’ নামে একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। যারা পরিচালনা করছে ৩৩টি খামার। এটিই পৃথিবীর আজকের বাস্তবতা।
কৃষির অগ্রগতি তখনই দ্রুত হবে, যখন নগরের মানুষ এর গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ আমাদের নীতিনির্ধারকরা মূলত নগরবাসী। নগরবাসী ও নতুন প্রজন্মকে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে আমার অন্যতম প্রয়াস ‘ফিরে চল মাটির টানে’। নাগরিক শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কৃষিশিক্ষার পাশাপাশি যার যার বিষয় ও অবস্থান থেকে কৃষির জন্য অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করাই এর বড় উদ্দেশ্য। বছর পাঁচ আগে তারই এক দৃষ্টান্ত গড়েছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী বি এম তাহাম্মুুল কবীর। তিনি তার ১৪ সপ্তাহের গবেষণায় তুলে ধরেন আগামীর নগরায়ণের সঙ্গে কৃষিকে অপরিহার্যভাবে নিয়ে আসার বিষয়টি। তার ধারণার শহরটির নাম ‘অ্যাগ্রোপলিস’। সেটি ছিল পুরোপুরি একাডেমিক গবেষণা উপস্থাপনের একটি সেশন। সুপারভাইজার প্রফেসর ড. খোন্দকার শাব্বির আহমেদের আমন্ত্রণে সেই গবেষণার একজন জুরি হিসেবে যুক্ত ছিলাম আমি। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ দেশের খ্যাতিমান স্থপতি ও শিক্ষার্থীরা। গবেষণা উপস্থাপনের পর উপস্থিত জুরিরা তাদের মতামত রাখেন। তারাও উপলব্ধি করেন নগরকৃষির গুরুত্ব। স্থাপত্যকলার দিক থেকে নানা পরামর্শ দেন। এ প্রজন্মের শিক্ষার্থী তাহাম্মুল কবীরের উপস্থাপিত গবেষণা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যে আগামীর কৃষি নিয়ে ভাবছে এটাই দারুণ বিষয়। তাহাম্মুল দূষণমুক্ত এবং নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নগরের কথা চিন্তা করছেন। এর জন্য বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ধান চাষের কথা বলছেন। কিন্তু কৃষির হরাইজন্টাল বা দিগন্ত জোড়া সম্প্রসারণ আমাদের পক্ষে এখন আর করা সম্ভব নয়। কারণ জমি বাড়ছে না। আনুপাতিক হারে কমছে কৃষিজমি। তাই ভার্টিক্যাল সম্প্রসারণের কথা ভাবতে হবে। গবেষণালব্ধ আধুনিক নগর পরিকল্পনা বা আবাসনব্যবস্থার সঙ্গে কৃষি উৎপাদন, নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা পূরণ, কার্বণ নিঃসরণ কমানোসহ সামগ্রিক চিন্তাটি নিয়ে তাহাম্মুল কবীরের সঙ্গে কথা বলেছি। তাহাম্মুল জানান, তার এই গবেষণার পেছনে রয়েছে মায়ের অনুপ্রেরণা। কথা হয় তাহাম্মুল কবীরের মা রাজিয়া কবীরের সঙ্গেও। তিনি জানান, চ্যানেল আইয়ের ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক’ অনুষ্ঠানের ছাদকৃষি দেখে নাগরিক জীবনে কৃষির উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন তিনি।
ছাদকৃষি, নাগরিক কৃষিরই এক অভিযান। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণমাধ্যমে যে অভিযানের চিত্র উঠে আসতে থাকে। আর বর্তমান সময়ের বহুমুখী উপযোগিতাকে চিন্তা করে গত তিন বছর ‘ছাদকৃষি’ চলছে চ্যানেল আইতে হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে। এই সময়ের মধ্যে সারা দেশে আবাসনের সঙ্গে কৃষি সমন্বিতভাবে চালিয়ে যাওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে। উদ্বুদ্ধ হয়েছে দেশে-বিদেশে অসংখ্য মানুষ। এরই এক রকমের ফলশ্রুতি তাহাম্মুল কবীরের আধুনিক নগর পরিকল্পনা ‘অ্যাগ্রোপলিস’।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গোটা পৃথিবীতেই আজ যে চ্যালেঞ্জ দানা বাঁধছে, তা হচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য। যে হিসেবেই আমরা ২০৩০-এর মধ্যে পৃথিবীকে ক্ষুধামুক্ত করার চিন্তা করি না কেন, পরিকল্পিত নগরায়ণ, বিশুদ্ধ নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা আর কৃষকসহ সব মহলের সমান অংশীদারত্বের ভিত্তিতে একটি বাস্তবমুখী কৃষি ও আবাসন পরিকল্পনা না করতে পারলে এই স্বপ্ন পূরণ করা কঠিন হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই নতুন প্রজন্মের ভাবনাগুলোকে মূল্যায়ন করার যৌক্তিকতা রয়েছে। আশা করা যায়, এই দৃষ্টান্তগুলোর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ে সময়োপযোগী গবেষণাসহ নানামুখী কাজ অব্যাহত থাকবে, অর্জিত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।
লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব