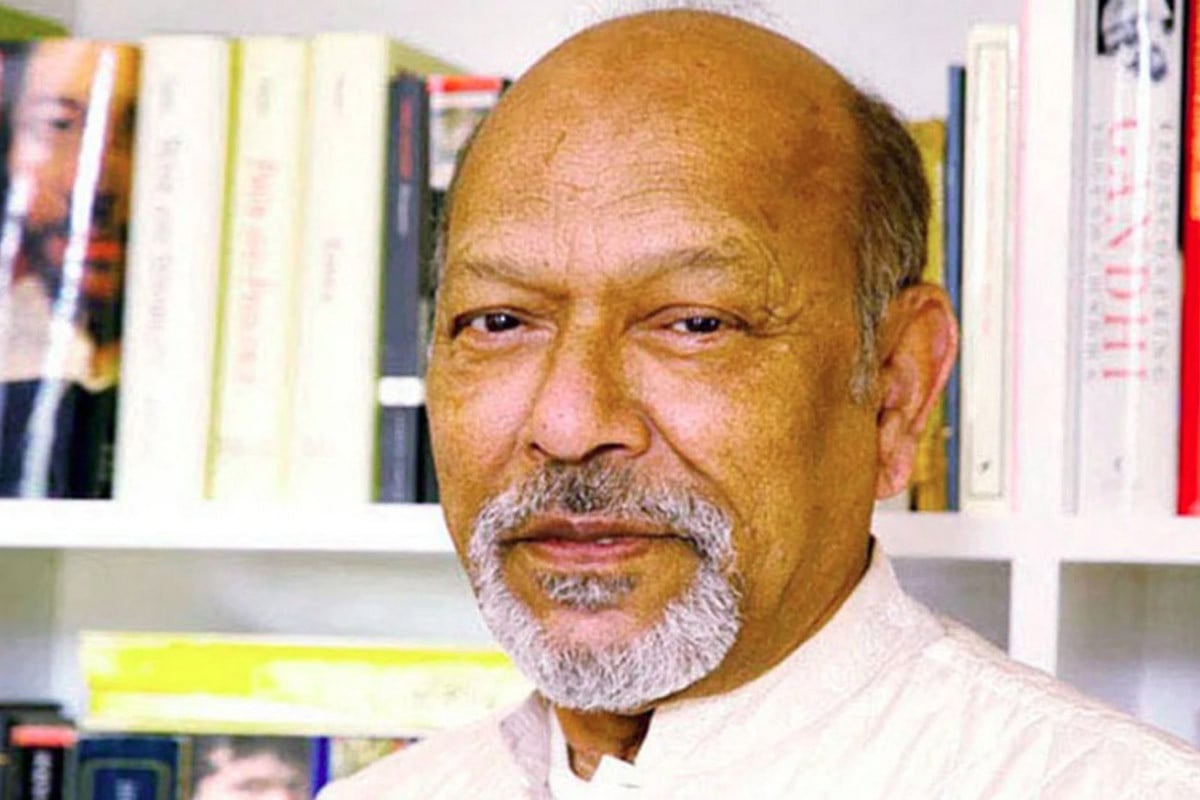গত ৪ আগস্ট 'দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে' চোখ রাখতেই সবার আগে একজন আত্মহত্যাকারীর ছোট্ট একটি সুইসাইড নোট আমার নজর কাড়ে। বরিশালের উদীচীর বাচিক শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী নিপা আত্মহত্যা করেছে। পঁচিশ বছর বয়সী উচ্চশিক্ষিতা এ নারী আত্মহত্যার পূর্বে লিখে গেছেন, "ব্যস্ত দুনিয়ার সবাই আবার ব্যস্ত হয়ে যাবে"। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং চিরায়ত। তার মৃত্যুর রহস্য হয়তো দ্রুত উদঘাটিত হবে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে প্রতিদিন গড়ে ২৯ জন আত্মহত্যা করে। বছরে প্রায় পনের হাজার। পৃথিবীতে বছরে ৯ লাখ এবং প্রতি সেকেন্ডে একজন। মানুষ নিজের জীবনকে নিজেই শেষ করে দিতে পারে। এটা কী ভাবা যায়? এটা কী এতো সহজ কাজ?
গবেষণা বলে, অন্যকে হত্যা করার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি সাহস লাগে নিজেকে হত্যা করতে। এবং অতি মেধাবী ও সাহসীরাই আত্মহত্যা করতে পারে। আত্মহত্যা বোধকরি, পৃথিবীর সমান বয়সী এক আদিম ব্যাধির নাম। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সূচনা এবং বিপরীতক্রমে মানুষ তার নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করতে শেখা একই সঙ্গে ঘটে। এটা ধ্রুব সত্য যে, মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। এর সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা হয় না। এটা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণিও নিজেকে সর্বাগ্রে রক্ষা করার কলাকৌশল রপ্ত করতে শেখে। এটাও মানুষের মত প্রকৃতিগতভাবেই প্রাপ্ত। কথায় বলে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। নিজের জীবনের প্রশ্নে মানুষ নাকি সব সময় অন্য প্রাণির চেয়ে স্বার্থপর। কেউ মরতে চায় না। সুন্দর মায়াবী এ ভুবন ছেড়ে চলে যেতে চায় না। শেষ মুহূর্তের হৃদস্পন্দন পর্যন্ত আশায় বুক বেঁধে থাকে। এই তো আমি বেঁচে আছি। জীবন এতো স্বপ্নময়, এতো মধুর যে, এর মোহে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে সবাই। তবু প্রতিদিন বিস্ময়াহত হয়ে দেখি, পত্রিকার পাতা জুড়ে আত্মহত্যার সংবাদের ছড়াছড়ি। কী বিচিত্র, বিভৎস মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে চলেছে মানুষ। প্রশ্ন জাগে কেন আত্মহনন, কারা করে, কখন করে? এটাকে কী প্রতিরোধ করা যায়? নাকি একেবারেই অবশ্যম্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্য পরিণতি?
২) মনে পড়ে, আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে আমাদের বন্ধু ফরহাদ আত্মহত্যা করে। সে তখন একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। এক সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র হিসেবেও তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ছিলেন। একই স্কুল এবং কলেজে পড়ুয়া আমরা খুবই সমসাময়িক ছিলাম। উভয়ই মধ্যবিত্তের সরাসরি প্রতিনিধি হলেও মনন এবং প্রতিভায় ফরহাদ আমাদের চেয়ে খানিকটা অগ্রসরমান ছিল। এর বাহ্যিক প্রকাশ তার আচরণের মধ্যে বিকশিত ছিল। এ কারণে তার ওপর পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা প্রচ্ছন্ন বাড়তি প্রত্যাশাও ছিল। যা তার আত্মহননের মধ্যদিয়ে চির সমাপ্তি ঘটে।
আজো স্মৃতিতে স্পষ্ট এবং ভাস্বর হয়ে আছে। তার আকস্মিক অকাল প্রয়াণে আমি মানসিকভাবে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলাম। কারণ ঢাকার একটি অভিজাত হোটেল-কক্ষের ফ্যানের সঙ্গে তার ঝুলন্ত দেহ খানা পুলিশের পরে সম্ভবত আমিই প্রথম দেখি।
তার সঙ্গে থাকা টেলিফোন ইনডেক্স জাতীয় ছোট্ট নোট বই থেকে তখন আমার অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়ের ফোন নম্বর পেয়ে পুলিশ আমাকেই প্রথম অবহিত করেছিল। তারা আমাকে তার অসুস্থতার কথা বলেছিল। আমি সেদিন নিঃসংশয়ে পল্টনের সেই বহুতল হোটেলে হাজির হলে উপস্থিত একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের স্বভাবসুলভ জেরার মধ্যে পড়ি। পরে তাকে নিয়ে হোটেল কক্ষে গিয়ে ফ্যানের সাথে দোদুল্যমান মরদেহ দেখে শিহরিত হয়ে চমকে উঠি। আমি হতচকিত অপ্রস্তুত হয়ে যাই। যে দৃশ্য আজও আমাকে চমকায়, তাড়িত করে এবং বেদনাহত করে। সেদিন আমি ঢাকায় তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নাম ও পরিচয় পুলিশকে জানালে তারা পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা এবং তার মৃতদেহ যথারীতি সৎকারের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছিল।
উল্লেখ্য, তখন তার এক মামা ঢাকা মেট্রো পুলিশেই ঊর্ধ্বতন কর্মকতা ছিলেন।
৩) মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ফরহাদকে প্রচণ্ড সন্দেহপ্রবণ, সংশয়বাদী ও অস্থিরতায় পেয়ে বসেছিল। তার কথা বার্তায় অসংলগ্নতা, অযৌক্তিকতা বা অবৈজ্ঞানিকতা মারাত্মকভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। অনেক দিন ঢাকার রাস্তায় দু'জন হেঁটেছি। অপরাহ্ন থেকে সন্ধ্যা অবধি সায়দাবাদ, টিকাটুলি, বলদাগার্ডেন ইত্যাদি এলাকায় ঘুরেছি। সে সময় তার অনবরত অবিবেচক কল্পলোকের ভাষ্য আমাকে ভাবিয়ে তোলে। এমনকি বন্ধু-বান্ধব বা নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে তার বিষোদগার ও অমূলক মন্তব্য খুবই অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। জানি সে কলেজ শিক্ষক। কিন্তু ঘন ঘন কলেজ বদল করার নেশায় পেয়েছিল তাকে। বাস্তবতা হলো, সে কোথাও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। এক স্থান থেকে অন্যত্র। রাতারাতি তাড়াতাড়ি এবং নিভৃতে ঠিকানা পরিবর্তন করে বোহেমিয়ান জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শগত বা সামাজিক দর্শনগত কারণেও আর দশজনের সাথে গা ভাসিয়ে চলতে পারছিল না সে। কোনো কর্তৃপক্ষের তোয়াক্কা না করার এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা পেয়ে বসে তাকে।
ঢাকায় বসবাসরত আপন বড় ভাইকে, ভাবীকে সন্দেহ করতো। নিজের বাবা-মাকেও আপন মনে করতো না। তার মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল, বাবা তাকে শৈশবে এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে দত্তক হিসেবে নিয়েছিলেন। তার প্রকৃত বাবা স্থানীয় এক বনেদি হিন্দু ব্যবসায়ী। এমনকি আপন বোনকেও সন্দেহের চোখে দেখতো। মোদ্দাকথা, দুনিয়ায় তার আপন বলে কেউ নেই। সবাই তাকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে চলে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে দুয়েকবার বাকবিতাণ্ডায়ও লিপ্ত হয়েছে সে। আহ! তার কী বিস্ময়কর যুক্তি ছিল! মাঝে মধ্যে হাসি পেতো, কষ্টও পেয়েছি তার এমন মনোবিকলন, এমন আকাশ-কুসুম ভাবনার জাল বিস্তার করে নিখুঁত শব্দ চয়ন দেখে।
মর্মাহত হয়ে নিজেও ভেবেছি, মাত্র বছর দুয়েক সময়ের ব্যবধানে এক তুখোড় মার্ক্সবাদী, সমাজতন্ত্রে বিভোর বস্তুবাদের ধারক যে নাকি মহামতি লেনিনের রণকৌশল, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ও ডাস ক্যাপিটল থেকে অনর্গল বলতে পারতো সে কিভাবে এমন অস্বাভাবিক ভাববাদীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল! এ কেমন আচরণ।
৫) একদিন বিকালে সে হন্তদন্ত হয়ে আমার টিকাটুলির দু' কামরার ছোট্ট বাসায় এসে হাজির। কিছুটা উৎকণ্ঠা নিয়ে বলছিল, তাকে কারা যেন দীর্ঘদিন যাবৎ অনুসরণ করে আসছে। তাকে সারাক্ষণ গোয়েন্দা সংস্থাও ফলো করছে। তাকে কারা যেন মেরে ফেলতে চায়। অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে সে পকেটে একটা পেপার ওয়েট রেখেছে। তার পকেটে পেপার ওয়েট বহন করার কাহিনী আমাদের আরেক বন্ধু জাহাঙ্গীরও একবার আমাকে বলেছিল।
আমি বললাম, এসব কী বলছো? কল্পনা বিলাসিতা ছাড়। বসো চা নাস্তা খাও। আমি তোমার সঙ্গে বের হচ্ছি। দেখি কোথায় কারা তোমাকে ফলো করে? তখন সে আরও বিচলিত বোধ করতো। ভাবছি আমাকেও আবার সন্দেহ করা শুরু করে কিনা। আমারও চাকরি জীবনের শুরুর সময়। বৈষয়িক কোনো বোধ তখনও জাগ্রত হয়নি। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে দু'জন মতিঝিলের দিকে যাচ্ছি। দৈনিক জনকণ্ঠ অফিস ছিল সেখানে। এবার তার সাংবাদিকতার নেশা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগরের একজন অগ্রজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। হঠাৎ নিঃশঙ্কোচে এবং বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ফেললো, 'আত্মহত্যা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল জায়গাটা খুব সুন্দর হবে- কী বলিস্! সকাল বেলায় এসে ছেলে-মেয়েরা দেখবে তরতাজা উপুড় হয়ে পড়ে আছি আমি, বেশ মজাই হবে, তাই না'?
আমি হতভম্ব। কি এসব বলছো তুমি?
সে বলে, না এমনি বলছি।
তুমি তো পত্রিকার চাকরির জন্য যাচ্ছো। পাগলামি করো না প্লিজ।
তুমি চাইলে অনেক কিছু করতে পারবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার সে বললো -- শোন,
'একদিন ভরা জোছনারাতে আমি ওখানটায় গিয়েছিলাম। দেখি ধবধবে ফর্সা আলো ছড়িয়ে আছে কার্জন হলের মূল ফটকের চারপাশে। মধ্যরাতেও গাছের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলো আর বিদ্যুতের আলোয় একাকার সবকিছু। রাতটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু বাধ সাধে দু'জন কর্তব্য পরায়ন নৈশপ্রহরী। বার বার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছিল এতো রাতে এখানে কী করছেন? পরিচয় কী- এসব। আমি নিরুত্তর থেকে একটু অপেক্ষা করে ফিরে আসি। সেদিন সময়টা মোটেই অনুকূলে ছিল না।
তার এমন দুঃসাহসিক অকপট বর্ণনা শুনে আমি খানিকটা ঘাবড়ে যাই। যদিও তাকে বুঝতে দিই নি। ভেতরে ভেতরে ভয় হচ্ছিল। আবার ভাবছিলাম, সে তো সব সময় এভাবেই বলে। একটা কাজে ডুবে গেলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
কী আশ্চর্য! জানা যায়, ১৯৬১ সালে মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে আত্মহত্যার পূর্বে নোবেলজয়ী ও আমেরিকান বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একই আচরণ করতেন। তিনি তার বন্ধুদের বলতেন দ্যাখ, চারপাশে কত গোয়েন্দা ঘুরছে, তারা আমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছে না। বাথরুম থেকে ব্যাংক সর্বত্র আমার পেছনে। মধ্যরাতেও আমি নিরাপদ নই। এভাবে বাঁচা যায় তোমারাই বল? বন্ধুরা বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিক গুপ্তচর খুঁজতো। কাউকে পেতো না। শেষ পর্যন্ত হেমিংওয়ে মুক্তি নিল পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া পিস্তলের পর পর দুটো বুলেট ব্যবহার করে। যিনি নাকি দুনিয়ার মানুষকে বলে গেছেন, "মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে,পরাজিত হতে পারে না"। তিনি নিজেকে ধ্বংসই করেছিলেন।
আর ১৯৬১ সালেই জন্ম নেয়া আমাদের মেধাবী বন্ধু, চৌকস ও বাগ্মী ফরহাদ প্রিতম হোটেলের চারতলার এক নির্জন কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে কণ্ঠ বেঁধে মাত্র ৩৫ বছরের জীবনকে বলে দিল 'না'। তবে তার কোনো সুইসাইড নোট ছিল না। ঝুলে থাকা শরীরের নিচে বিছানায় একটা উন্মুক্ত বলপেন আর সাদা প্যাড পড়ে ছিল। যাতে কালির আঁচড় লাগেনি।